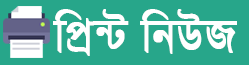ভূমি সংস্কার ও আদিবাসীদের উন্নয়ন; তপন দেববর্মা

আদিবাসী মানুষের জীবন ও জীবিকা সহজ-সরল। আদিবাসীদের জীবন এদেশের মাটি ও প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। আদিবাসীদের কথায় বলা যায় "Land is Life, Life is Land" অর্থাৎ প্রকৃতিই আদিবাসীদের জীবন। মাটি, জল, বায়ু, আলো, বন, গাছপালা ইত্যাদ্দির সঙ্গে আদিবাসীদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রণালী ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছে এদেশকে। পরিসংখ্যান বলে, বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩০ লক্ষ। বাঙালী জাতি ছাড়াও কমপক্ষে আরো ৪৫টি আদিবাসী আতি বসবাস ভরছে এদেশে। দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও পৃথিবীর অনেক দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এটি বেশী। বাংলাদেশের সরকারি কাগজে আদিবাসীদের পরিকল্পিতভাবে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আমরা সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং অন্দতার কারণে আদিবাসীদের 'উপজাতি' বলতে অভ্যন্ত হয়ে গেছি। এই পরিস্থিতি অমর্যাদাকর এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী। আমরা এখনো এই অবস্থা থেকে বের হতে পারিনি।
প্রখ্যাত গবেষক ডঃ তপন কুমার দে বলেন ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন, 'অসম ভূমি মালিকানার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির পুণর্বণ্টন শুধু যে মানুষের জীবন ও জীবিকার সংস্থান করবে তা নয়, এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা সৃষ্টি করবে, কারণ এটা জমির জন্য তাদের আকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করে, সহযোগিতা গড়ে তোলার মতো ন্যূনতম আর্থিক বুনিয়াদ সৃষ্টি করে, অসমতা কমিয়ে আনে এবং অধিকতর সৌভ্রাতৃত্বের জন্য দেয়। শেষ পর্যড় এই মনোভাব সম্পদের সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যবহারের দিক নির্দেশনা দিতে পারে- ভূমি সংস্কারের পূর্ববর্তী অবস্থায় যা কিছুতেই সম্ভব হয় না।' তাই কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন ভূমি সংস্কার দরকার, তেমনি সমতল ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের উন্নয়নেও প্রয়োজন তাদের প্রথাগত রীতি-নীতি বজায় রেখে আদিবাসীদের জন্য প্রচলিত বা প্রণীত আইনী বিধানের আলোকে তাদের ভূমি সমস্যার সমাধান করা। সঠিকভাবে আদিবাসীদের চাষযোগ্য জমি তাদের মাঝে বণ্টিত হলে এবং একটি আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলেই আদিবাসীদের নিজ জমি ফিরে পাবার তীব্র আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হবে, গড়ে উঠবে বাঙ্গালী আদিবাসী যৌথ সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। ফলে আদিবাসী সমাজে সৃষ্টি হবে আর্থিক বুনিয়ান, অসমতা হ্রাস পেয়ে জন্ম নিবে অধিকতর সৌভ্রাতৃত্ব। পাল্টে যাবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট জাতিবৈরিতার বর্তমান চেহারা, সার্বিকভাবে দেশে উন্নয়নের চাকা হবে সচল।
ভূমি-কেন্দ্রিক আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও আর্থ সামাজিক কাঠামোর কথা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সামাজিক অগ্রগতির কথা ভাবলে সমতল ও পাহাড়ী আদিবাসীদের ভূমি হস্তস্তর, মালিকানা নির্ধারণ ও সর্বোপরি ভূমি-ব্যবস্থাপনায় যে স্থবিরতা, অচলাবস্থা, জটিলতা, বৈষম্য ও অনাচার যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে তার অবসান ঘটানোর কোন বিকল্প নেই।
লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় 'আদিবাসীদের কথা' প্রসঙ্গে বলেছেন- 'আদিবাসীরাই এদেশের আদিম অধিবাসী। যখন আর্যভাষীরা এ দেশে ছিলো না তখন সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা প্রভৃতি ট্রাইবগুলো ছিল। এরা এতদিন টিকে আছে, তাঁর কারণ এরা বাঘ ভালুকের মতো জঙ্গলে বাস করতো। বনে বাস করলেও সেখানে জুম পদ্ধতিতে চাষ করতো। এখন এসব স্থানে জুম চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল সাফ করে নদীর জলে গাছগুলো ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেশকে শিল্পায়িত করতে গিয়ে বন জঙ্গলে হাজার হাজার আদিবাসীর নিরাপদ আশ্রয় ধ্বংস করা হচ্ছে। জলের মাছ ডাঙ্গায় বাঁচে না। তেমনি আদিবাসীরাও চারিদিকে গজিয়ে ওঠা শহর বা শহরতলিতে বাঁচবে না। প্রাণ ধারণের জন্য যা যা দরকার তা ঘাটতি হলে পূরণ করবে কে? কি কি দিয়ে?
বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও কনভেনশন-১০৭ এর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আদিবাসী জনগণের আবাসনের জন্য জমি-জমার কোনো কাগজের প্রয়োজন হয় না। আদিবাসীদের বংশ পরম্পরায় বসবাস করার ইতিহাসই তার কাগজ। তবুও প্রতিনিয়ত কাগজপত্র না থাকা এবং বহিরাগত ভূমিদস্যু এবং বন বিভাগের আগ্রাসনে ভূমি হারানোর ভয়, নারী ও অন্যান্য সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা তাদেরকে প্রতিনিয়ত আতংকগ্রস্ত করে তুলছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী আজো প্রশাসনের এক শ্রেণীর অসাধু লোকজনের সহায়তায় ছলে-বলে-কৌশলে জাল দলিল, মিথ্যা মামলা, ভয়-হুমকি দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত সম্পদ ও চাষযোগ্য জমিগুলো। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। দিন দিন এটি ত্বরান্বিত হচ্ছে। আদিবাসীরা এসব অপকর্মের সাথে পরিচিত নয়। তারা নিভৃতে চোখের জল ফেলছে, বুকে চাপা যাথনা নিয়ে দিনাতিপাত করছে। এ ছাড়াও সরকারের প্রণীত অর্পিত সম্পত্তি আইনের মতো কালো আইনের থাবায় সমতলের আদিবাসীদের সম্পত্তি সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেদখল হয়েছে।
দেশে আদিবাসীরা ভূমি অধিকার ও ভূমি রক্ষা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে লড়াই, সংগ্রাম করে আসছে। কখনো কখনো এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তুমি গ্রাসীদের হথতি বন্ধ করা গেলেও সাজানো মামলা থেকে মুক্তি পায়নি আদিবাসীরা। এচলিত আইনী কাঠামোতে এসব মামলা পরিচালনার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা আদিবাসীদের নেই। মামলা করতে গিয়ে আদিবাসীরা আজ বিষ হয়ে পড়েছে। বর্তম্যান প্রশাসনের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতার অভাবে আইনের বিধান বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রশাসনের উপর তাদের আস্থাহীনতা আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে আইএলও কনভেনশন রেটিফাই করার পরও এ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে আদিবাসীদের কল্যাণে ভূমি আইন সংস্কার হয়নি। ইতিহাস বলছে, আদিবাসী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীতে যত জাতিসত্ত্বা আছে তারা নিজ নিজ জায়গাতে অনাদিকাল থেকেই স্থায়ী বাসিন্দা। ক্রমবর্ধমান বাঙালী আধিপত্যে সর্বত্র আদিবাসীদের অবস্থা এখন প্রান্তিক পর্যায়ে। পাহাড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় সুযোগ পাচ্ছেন না আদিবাসীরা। যেমন- সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি উপজাতীয় ইনস্টিটিউটে পাহাড়ি নাচের শিক্ষক হিসেবে তালিম দেবেন একজন বাঙালি নৃত্যশিল্পী। আজকে আমরা দেখছি- পাহাড়ী এলাকার ভূমির সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, যারা পাহাড়ের গাছপালাকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য নষ্ট করছে, প্রতিনিয়ত গাছ কেটে উজাড় করছে বন, দখল করে নিচ্ছে চাষের জমি ও সম্পত্তি, আদিবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে, বাঙালী জাতি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। আদিবাসীরা বছরের পর বছর বসবাস করলেও তাদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি এ দেশে। গারো ও খাসিয়াদের উচ্ছেদ করে এখনো পরিকল্পনা হচ্ছে ইকো-পার্ক নির্মাণ প্রকল্পের। অথচ ভিন্ন কথা বলছে আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো।
জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক অধিকার সনম এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক সনদের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, সকল জনগোষ্ঠীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সে অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে। জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক খসড়া ঘোষণাপত্রের তৃতীয় ধারাতেও একই কথা বলা হয়েছে। ইতিহাস বলে, ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের জীবনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল। কেউ কেউ ব্রিটিশ আমলে বা তার আগেও সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত জীবন যাপন করতো। বর্তমানে আদিবাসীদের আত্ম- নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বললে অনেকে শংকায় ভোগেন। ঔপনিবেশিক মানসিকতার ক্ষমতাদর্শী ও নিয়ন্ত্রণকামী সমাধান প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। অধিকারভিত্তিক সমাধানই জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার স্বীকৃতিসহ আদিবাসীদের সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রের সীমানা ও পরিধির মধ্যেই পাহাড়ী আদিবাসী মানুষের জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ গ্রহণ সম্ভব। এমনকি দেশের সমতলের আদিবাসীদের সীমিত পরিসরে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দরকার। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আদিবাসীদে ভূমি, মাটি, বন ইত্যাদি সম্পদ ও তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসা দরকার। এক কথায় বলা যায়, আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে- আদিবাসীদের উন্নয়ন তথা দেশের স্বার্থে প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ট বাঙালি জনগণের হৃদয়ের পরিবর্তন। প্রথমে ব্যক্তি মানুষের, সেখান থেকে যা ছড়াবে সমাজের অভ্যন্তরে। পরিবেশে ব্যক্তি ও সমাজের দাবিতে ও চাপে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে। নতুবা আদিবাসীরা কেবল তাদের সাংস্কৃতি প্রতীকে টিকে থাকবে, রক্ত মাংসের বাস্তব আদিবাসীদের দেখা মিলবে না। কালক্রমে তাও হারিয়ে যাবে। এই ধ্বংসে নৈতিক দায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরই থেকে যাবে।
তাই আমাদের প্রত্যাশা- অবিলম্বে বাংলাদেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং পাহাড়ী এলা জন্য গঠিত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর এবং সমতল এলাকার আদিবাসীদের জন্য আরেকটি ভূমি বিজ্ঞ কমিশন গঠন করাসহ তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা হোক।
লেখক ড. তপন দেববর্মা
যুব অর্থনীতীবিদ
দ.ক.মতামত
© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত